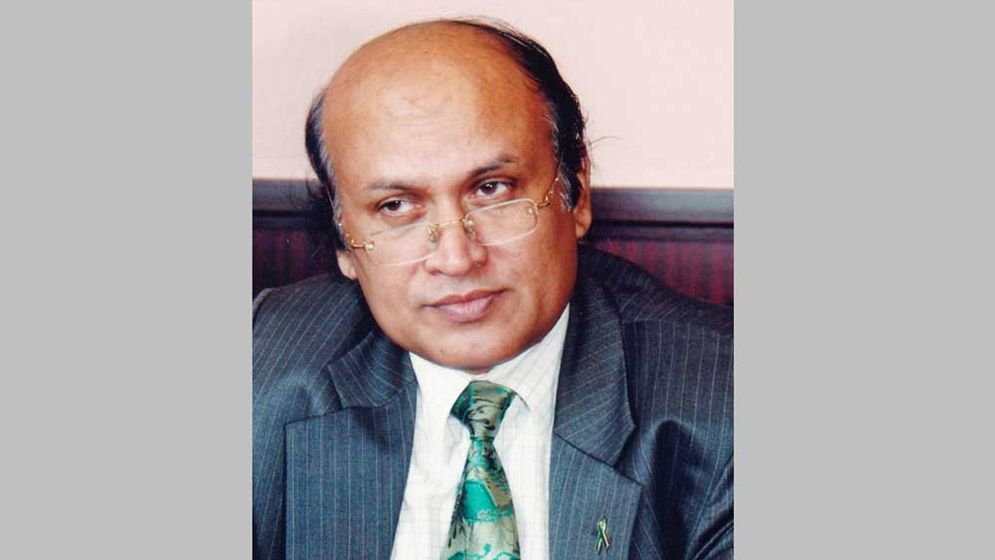শিক্ষা কার্যক্রমে চলচ্চিত্র পাঠ জরুরি কেন?
-

- - নিজস্ব -
- প্রতিবেদক --
- ২২ অক্টোবর, ২০২৫
একটা সময় ছিল, যখন ছেলেমেয়েরা ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখতে যেত। এখন এই নতুন যুগে সিনেমাই সদর্পে ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ছে। একে তো বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমাধ্যমের সহায়তায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তার ওপর ভালো চলচ্চিত্র যে মনন গঠনে চমৎকার ভূমিকা রাখে সেটাও আজ কেউ অস্বীকার করে না। নতুন প্রজন্মের শিক্ষকদের ভেতর চলচ্চিত্র দেখার চর্চা আগের প্রজন্মের চেয়ে বেশি। তাই তারা চলচ্চিত্রের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।
সেজন্যই বোধহয়, বাংলাদেশের কয়েকটি বিদ্যায়তনে ইদানীং চলচ্চিত্র দেখানোর চল শুরু হয়েছে। তবে সেটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এদেশে নিয়মিত চর্চার অংশ হিসেবে এখনো চলচ্চিত্র দেখানো হয় না শিক্ষার্থীদের। দেশের বাইরে কিন্তু এই চর্চা শুরু হয়েছে গত শতক থেকেই।
১৯৯৪ সাল থেকে ফ্রান্সের ‘একোল এ সিনেমা’ কার্যক্রমের আওতায় স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ধ্রুপদি ও সমসাময়িক ভালো চলচ্চিত্র প্রদর্শন সংযুক্ত করা হয় জাতীয় শিক্ষাদান কর্মসূচিতে। যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের আছে ‘ইনটু ফিল্ম’ কার্যক্রম, এর মাধ্যমে ওরা স্কুলগুলোয় গল্প বলার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের ইতিহাস সচেতন করে তোলে এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান জানাতে শেখায়।
ভারতেও স্কুলে ছবি দেখানোর চল রয়েছে, অনিয়মিতভাবে হলেও। তাদের জাতীয় দুই প্রতিষ্ঠান, পুনেতে অবস্থিত ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট ও ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ বিদ্যালয়গুলোয় গিয়ে বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। যেমন সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা জাগ্রত করার জন্য প্রদর্শন করে ‘তারে জামিন পার’, দেশপ্রেম বিষয়ে সচেতন করতে তারা দেখায় ‘স্বদেশ’।
চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যের কারণেই, শিশু থেকে বৃদ্ধ এই শিল্পের রস আস্বাদন করে নিবিড়ভাবে। আর এর মাধ্যমে শিশুকিশোরদের দেশের শুধু নয়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানানো যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাঠ্যবইয়ে কারও জীবনী পড়ানোর পাশাপাশি দেখানো যেতে পারে বায়োগ্রাফিকাল ফিল্ম।
ধরুন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অথবা নেপোলিয়নকে নিয়ে কোনো অধ্যায় শেষ করার পর তাদের ওপর নির্মিত কোনো প্রামাণ্যচিত্র দেখানো গেলে, তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আরও গভীরভাবে জানতে পারবে। আবার কোনো সাহিত্যকর্ম পাঠের আগে, সেই সাহিত্যকর্মকে নির্ভর করে কেউ যদি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকেন, তাহলে সেটি দেখালে, শিক্ষার্থীরা দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়বে। যেমন ‘আম আঁটির ভেঁপু’, যা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’র ছোটদের সংস্করণ, সেটি পড়ানোর পাশাপাশি যদি সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ দেখানো যায়, তাহলে সেই পাঠদান হবে সর্বাঙ্গীনভাবে পরিপূর্ণ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অবস্থা কেমন ছিল, ইতিহাসের এই পাঠদানের আগে, বাচ্চাদের যদি শ্রেণিকক্ষে ভিত্তোরিও ডি’সিকার ‘বাইসাইকেল থিভস’ দেখানো যায়, শ্রেণিকক্ষ আরও আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে বাধ্য। এই পাঠদান শিক্ষার্থীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হবে।
প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, সেখানে তো চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পাঠদানের সুযোগ অবারিত। প্রতিষ্ঠান চাইলেই কাজটি করতে পারে এবং এতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকতে আগ্রহ বোধ করবে। উপস্থিতির জন্য আলাদা করে দশ নম্বর ধরে রাখতে হবে না। ইতিহাস থেকে অর্থনীতি, সাহিত্য থেকে পদার্থবিজ্ঞান, এমনকি গণিতশাস্ত্র, সব ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্র হতে পারে অতিগুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শিক্ষা উপকরণ।
শুধু দেখানোতে সীমাবদ্ধ না থেকে, হাতে কলমে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে, একদিকে ছেলেমেয়েরা যেমন প্রশংসা করার উপযোগী বা যোগ্য হয়ে উঠবে অর্থাৎ অ্যাপ্রিসিয়েশন বা প্রশংসা করতে শিখবে, তেমনি নিজেরাও দক্ষ হয়ে উঠবে। যাকে আমরা বাড়ির কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বলি, সেই কাজটিও হতে পারে দৃশ্যমাধ্যমের দ্বারা উপস্থাপিত। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরই, এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট তাদের দেওয়া যায়।
আর এখন তো মোবাইল ফোন দিয়েই কত ধরনের কন্টেন্ট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাড়ির কাজের বিষয়টি বলি, ধরুন, লিঙ্গবৈষম্য বা অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে যদি গ্রুপ করে শিক্ষার্থীদের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানাতে বলা হয়, তাহলে তারা সেই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার অবকাশ পাবে এবং দৃশ্যমাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার ভেতর দিয়ে বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।
হাতেকলমে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল-কলেজগুলোয় ছোট ছোট কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রত্যেক ক্লাসে, বছরে অন্তত একবার করে এই কর্মশালা করাতে পারলে, দৃশ্যমাধ্যমের ভাষাটা ধীরে ধীরে তাদের আয়ত্তে আসবে। তাছাড়া, এই কর্মশালা কেবল যে তাদের নির্মাণে সহায়তা করবে তা নয়, বরং অন্য নির্মাণকে ভালো করে বোঝার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে। অর্থাৎ তারা দৃশ্যমাধ্যম-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। তাদের তখন জানা থাকবে ‘হাউ টু রিড অ্যা ফিল্ম’।
আজকে যখন সারা দুনিয়া ভিজ্যুয়াল কন্টেন্টের স্রোতে ভাসছে, তখন শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু করা উচিত ছোট বয়স থেকেই। এতে করে এই সত্যোত্তর বা পোস্ট ট্রুথের যুগে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যখন নানাবিধ সত্য-মিথ্যা-অর্ধসত্য সব মিলিয়ে-মিশিয়ে আধেয় বা কন্টেন্ট বানানো হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে; তখন এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দৃশ্যমাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে ওঠা শিশুরা সহজে ওসবে প্রতারিত হবে না, ধোঁকা খাবে না, এমনকি প্ররোচিতও হবে না।
তারা পার্থক্য করতে পারবে কোনটা প্রোপাগান্ডা, আর কোনটা শিল্প। তারা ধীরে ধীরে শিখে যাবে, কেমন করে রাজহাঁসের মতো পাখা থেকে ময়লা-কাঁদা ঝেড়ে ফেলতে হয়, দুধ থেকে পানিকে আলাদা করতে হয়। তারা বুঝবে কে কোন ধ্বনিচিত্রের আধেয় দিয়ে কোন মতাদর্শ প্রচার করছে। এবং সেই মতাদর্শকে কীভাবে ধ্বনিচিত্রের আধেয় দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়, সেটাও তারা শিখে নেবে কৈশোর থেকেই।
আমরা টিকটক, ফেসবুক ও ইউটিউবের যুগে বাস করি। এই যুগে প্রায় সবাই রিলস বা ছোট ছোট আধেয় বানাতে বেশ পাকা। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না, কন্টেন্ট শুধু বানাতে পারলেই হয় না, সেটি একটি কৌশলগত দিক, এর পাশাপাশি যদি কেউ জানে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কীভাবে সারবস্তু সম্পন্ন আধেয় বানাতে হয়, তাহলে জঞ্জাল কন্টেন্টের পরিমাণ অনেক কমে যাবে।
আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট বানাবে এবং এর ভেতর দিয়ে জ্ঞানভিত্তিক সুস্থ সমাজ নির্মাণের পথ সুগম হবে। অডিও-ভিজ্যুয়ালের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই, এই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মাধ্যমকে কীভাবে ইতিবাচক উপায়ে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কিত শিক্ষার প্রয়োজন আছে বৈকি।
আর সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টি তা হলো শিল্পবোধ জাগ্রত করা। একটি সমাজে শিশুরা যখন শিল্পের সর্বশেষ শক্তিশালী মাধ্যমটির দ্বারা শিক্ষিত হয়ে বড় হতে থাকবে, সেই শিল্পের মর্মার্থ অনুধাবন করবে নানাবিধ বিষয়ের মাধ্যমে, তখন সেই সমাজ ধীরে ধীরে সংবেদনশীল ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষে ভরে উঠবে।
বিদ্যালয়গুলোয় যদি শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম—সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটক, অঙ্কন ইতি ও আদির নিয়মিত ক্লাস থাকতে পারে, তাহলে চলচ্চিত্র, যেটি শিল্পের সর্বশেষ ও শক্তিশালী মাধ্যম, সেটি কেন নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে না?
এই প্রশ্নটি নিয়ে, আধুনিক যুগে ধ্বনিচিত্রের সায়রে হাবুডুবু খাওয়া আমাদের, গুরুত্ব দিয়ে ভাবা ও আশু কর্তব্য নির্ণয় করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
1.gif)

.jpeg)
1.gif)
4.gif)